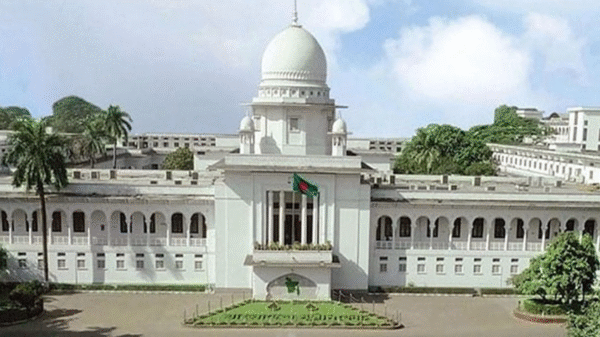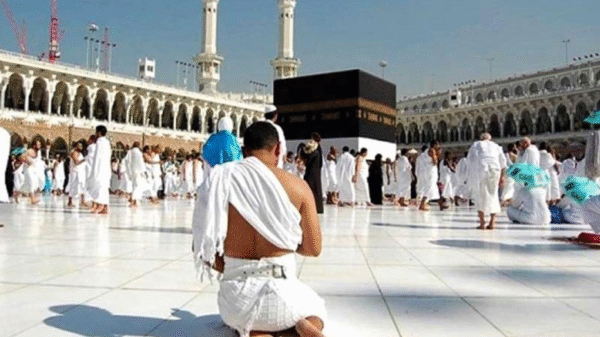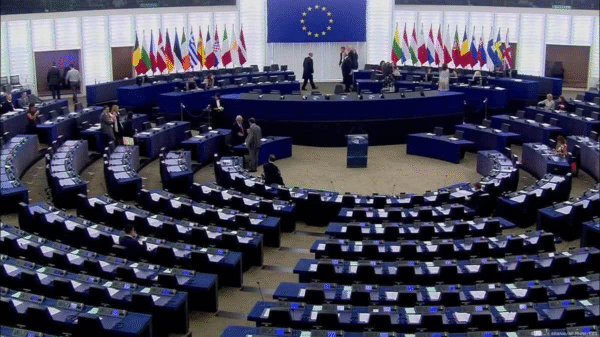ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

- আপডেট সময় শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ৫৪ বার দেখা হয়েছে

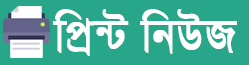
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের ইতিহাস শুধু গৌরব ও অগ্রগতির নয়, বরং নানা প্রতিবন্ধকতা ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামেরও। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই এর পথচলা ছিল কন্টকাকীর্ণ, কারণ এর প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা এসেছিল তৎকালীন কিছু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। তাদের এই বিরোধিতার মূল কারণ ছিল, পূর্ববঙ্গে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হলে তা মুসলমানদের শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়তা করবে—এমন আশঙ্কা। তাদের এই মনোভাব এমন ছিল, যেন মুসলমানরা যেন ন্যূনতম শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হয়! এটি ছিল তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশদের ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ (Divide and Rule) নীতির এক করুণ প্রতিফলন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা এতটাই জোরালো ছিল যে, তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান কয়েকজন প্রতিনিধি এবং হিন্দু সমাজের নেতারা স্বয়ং বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে দেখা করে এই পরিকল্পনা বাতিল করার দাবি জানান। তারা মনে করতেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে দেবে এবং বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করবে। এই বিরোধিতার পেছনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরও স্পষ্ট হয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহাস করে ‘Mecca University’ বলে কটাক্ষ করা হয়। এই ধরনের উপহাসের মাধ্যমে যেন এটি বোঝানো হচ্ছিল যে, এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল মুসলিমদের জন্য এবং এখানে আধুনিক জ্ঞানচর্চার কোনো সুযোগ থাকবে না।
রমেশ চন্দ্র মজুমদার, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের অন্যতম অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে উপাচার্য হয়েছিলেন, তিনি তার ‘ঢাকার স্মৃতি’ প্রবন্ধে এই বিরোধিতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, “তাদের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল যে এর ফলে রাজনৈতিক ভাগের পরিবর্তে বাংলাদেশকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই ভাগ করা হবে।”
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের শিক্ষিত মনোভাবের কারণে এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছিল। ব্রিটিশ শাসকরা এই অনুপস্থিতিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করে এবং বুঝতে পারে যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যদি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়, তবে তা ফরাসি বিপ্লবের মতো ভয়াবহ পরিণতি আনতে পারে। তাই তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনকে উৎসাহিত করে এবং পরবর্তীতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ, এবং পৃথক নির্বাচনের মতো বিভেদাত্মক নীতি গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের এই বিভেদ নীতিরই একটি অংশ।
অনাথবন্ধু বেদজ্ঞ তার ‘একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়’ লেখায় উল্লেখ করেছেন, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভেঙে দেওয়া। তিনি লেখেন, “হিন্দু মুসলমান মিলন তাদের রাত্রির নিদ্রা হরণ করল। তাই তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কর্মসূচী তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।” তার মতে, এই কর্মসূচীরই একটি অংশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
তবে সকল বাধা এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সত্যিকারের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। প্রথম উপাচার্য পি. জে. হার্টগ-এর দূরদর্শিতায় তিনি মেধাবী শিক্ষকদের একত্রিত করেন। এই শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের, যেমন—সত্যেন বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং হরিদাস ভট্টাচার্য। কিন্তু তারা নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষার্থীদেরকে শুধুমাত্র শিক্ষার্থী হিসেবেই দেখতেন। ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত রক্ষণশীল হলেও তারা তাদের অসাম্প্রদায়িকতার জন্যই বেশি পরিচিত ছিলেন। এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি দৃঢ় মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল, যা বহিরাগত সাম্প্রদায়িক বিভেদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি।
ফলস্বরূপ, উপহাসের ‘Mecca University’ না হয়ে এটি একটি ‘পাক্কা’ অর্থাৎ সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করে। এটি কেবল জ্ঞানের কেন্দ্রই হয়ে ওঠেনি, বরং ধর্মনিরপেক্ষতার একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে যা পরবর্তীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে।
(প্রতিবেদনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ২০২২ সালে ৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে প্রথম স্মারক বক্তৃতা ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ: বিচারের দুই নিরিখে’-এর আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে)