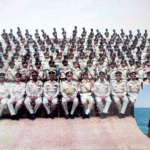গণতন্ত্রে জনসেবার ধারণা

- আপডেট সময় শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
- ১৯২ বার দেখা হয়েছে

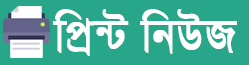
খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে? ধান ফুরালো, পান ফুরালো, খাজনার উপায় কি? আর কটা দিন সবুর কর, রসুন বুনেছি।
বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপি বাংলাভাষাভাষী ডায়াস্পোরায় বহুল প্রচলিত একটি লোকগাঁথা হচ্ছে উপরের এই ছড়াটি। এতে প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে যুগে যুগে রাজা কিংবা সম্রাটদের আমলে বিদ্যমান মধ্যসত্ত্বভোগী আমলাদের আচরণ ও দৃষ্টিভংগীর কথা। রাজা কিংবা তাদের মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে যুগে যুগে গরীব, শ্রমিক শ্রেণীর হাতে রচিত হয়েছে গান। ভারত উপমহাদেশে নাগরিকশোষণমূলক এমন কার্যক্রমেরই ফলাফল হচ্ছে ছিয়াত্ত্বরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ; ১৭৭০ খ্রি এবং ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ব্রিটিশদের প্রণীত সূর্যাস্ত আইন। এদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে সূর্যাস্ত আইনের কারণে শূধুমাত্র তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক স্বার্থে নির্ধারিত কর/খাজনা আদায়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের কারণে এদেশের কৃষক শ্রমিকরা জমির মালিকানা হারায় এবং নতুন জমিদাররা বেশি কর বা খাজনা প্রদান করে জমির মালিকানা লাভ করে। জমির মালিকানা চ্যূতির বিরলতম ঘটনা ঘটে তৎকালিন দস্যুরুপী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বৈরশাসক লর্ড কর্ণওয়ালিশ এর চালূ করা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রিটিশদের সূর্যাস্ত আইন। নির্ধারিত তারিখে কোন জমির নির্ধারিত খাজনা সূর্যাস্তের পূর্বে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে জমিচাষী কৃষক তো দূরের কথা সেই জমি সংশ্লিষ্ট জমিদারের মালিকানাও বাতিল করা হত, এবং সেই জমি নিলামে তুলে অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানায় দেওয়া হত। এ সকল কার্যক্রমে রাজা কিংবা সম্রাটদের হাতিয়ার ছিল সে সময়ের জনশোষকরুপী আমলাতন্ত্র। এরকম নাগরিক বিদ্বেষী ও নাগরিক অধিকার বিরোধী প্রেক্ষাপটেই গোটা দুনিয়ায় শোষিত মানুষের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে হাজির হয় গণতন্ত্র (ডেমোক্রেসি) ব্যবস্থা। এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধানতম মাত্রা হচ্ছে মানুষের অধিকার। মানুষ এবং মানুষের কল্যাণই হচ্ছে এই শাসন ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। গণতান্ত্রিক এই শাসনব্যবস্থার অনুষংগ হিসাবেই হাজির হয় নাগরিকবান্ধব আমলাতান্ত্রিক জনসেবা পদ্ধতির। বাস্তবায়নকেন্দ্রিক কিছু পার্থ্যকের কারণে জনকল্যাণের পার্থক্য থাকলেও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, গণতন্ত্র হচ্ছে মানব ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সর্বোচ্চ মানব-সৃষ্ট ঘটনা যাতে মানুষের অধিকারকে প্রথমবারের মত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। একে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত দেশে দেশে জনসেবাকে প্রাধান্য দিয়ে রিপাবলিক গঠিত হয়েছে এবং এসব রিপাবলিকের সংবিধান প্রণীত হয়েছে।
জনসেবা বা পাবলিক সার্ভিস এর ইতিহাস মানব-সভ্যতার ইতিহাসের মতোই পুরোনো। যুগে যুগে এর বিবর্তন ঘটেছে, যা সমাজের চাহিদা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। এটি শাসকের ব্যক্তিগত আদেশ পালন থেকে শুরু করে জনগণের কল্যাণে নিবেদিত একটি পেশাদার ও সুসংগঠিত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। জনসেবাকে সেবাপ্রদানকারীর ভিত্তিতে সরকারী সেবা (পাবলিক সার্ভিস) ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবা (ভলান্টারি সোশাল সার্ভিস)এই দু’ভাগে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের আজকের এই নিবন্ধে সরকারী জনসেবার বিকাশের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।
প্রাচীন যুগে জনসেবা
জনসেবার ধারণাটি প্রথম বিকশিত হয় প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে, যেমন—মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং রোমান সাম্রাজ্য। এই সময়ে জনসেবা বলতে মূলত শাসক বা সম্রাটের আদেশ পালন করাকে বোঝাতো। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা, কর সংগ্রহ, এবং সামরিক কার্যক্রমের জন্য জনবল প্রস্তুত করা। রোমান সাম্রাজ্যে জনসেবা একটি সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। তারা সড়ক নির্মাণ, পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে অ্যাকুয়াডাক্ট তৈরি এবং সামরিক অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জনসেবকদের নিয়োগ করতো। এসময় জনসেবকরা ছিল মূলত সম্রাটের প্রতি অনুগত এবং আমলাতান্ত্রিক পদে আসীন। প্রাচীনকালে জনসেবার ধারণাটি জনগণের অধিকার রক্ষার বদলে শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার একটি হাতিয়ার ছিল। এই কারণে প্রাচীনকালে জনগণের কাছে আমলারা ছিলেন ভয়ের প্রতীক, ভালোবাসার বা শ্রদ্ধার নয়।
মধ্যযুগ ও সামন্তবাদে জনসেবা
মধ্যযুগে জনসেবার ধারণাটি সীমিত হয়ে পড়ে। ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা ছিল ভূস্বামী বা অভিজাত শ্রেণির হাতে। জনসেবা তখন মূলত রাজার ব্যক্তিগত সেবা এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তিগত আনুগত্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে, চীনে জনসেবার একটি ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। হান রাজবংশের সময় (খ্রিস্টপূর্ব ২০৬-২২০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা চালু হয়, যা কন্ফুসিয়াস-এর দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য ও মেধাবী ব্যক্তিদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেওয়া হতো, যা আধুনিক আমলাতন্ত্রের পূর্বসূরি।
জনসেবায় আধুনিক যুগের সূচনা:
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাবে জনসেবার ধারণায় বড় পরিবর্তন আসে। রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু শাসনকার্য পরিচালনা নয়, বরং জনগণের কল্যাণে কাজ করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৭শ শতাব্দীতে প্রুশিয়ার (বর্তমানে বিলুপ্ত এবং জার্মানির সাথে যুক্ত) ফ্রেডরিক উইলিয়াম এবং ১৮শ শতাব্দীতে ফরাসি বিপ্লব জনসেবাকে একটি পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। এই সময় থেকে মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী সরকারি পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯শ শতাব্দীতে জনসেবা একটি পূর্ণাঙ্গ পেশাদার রূপ লাভ করে। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১৮৫৪ সালে ব্রিটেনে ‘নর্থকোট-ট্রিভিলিয়ান রিপোর্ট’ অনুসারে ‘সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট’পাশের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। এর আগে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হতো। এই পরিবর্তনের ফলে সরকারি পদে দলীয় আনুগত্যের বদলে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা প্রাধান্য পায়। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ‘পেনডেলটন সিভিল সার্ভিস রিফর্ম অ্যাক্ট’ (১৮৮৩) পাশের মাধ্যমে সরকারি নিয়োগে মেধাভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়। এর ফলে রাজনৈতিক নিয়োগের ‘প্যাট্রোনেজ বা স্পয়েল সিস্টেম’-এর অবসান ঘটে। ২০শ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং মহামন্দার পর জনসেবার পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। জনসেবা তখন শুধু প্রশাসন পরিচালনা নয়, বরং জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক গণতান্ত্রিক দেশ কল্যাণমূলক অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এই সময়ে অনেক রাষ্ট্র শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বেকার ভাতা এবং পেনশন স্কিমের মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করে। দার্শনিক হেনরি ফায়োল ও ম্যাক্স ওয়েবার-এর মতো চিন্তাবিদগণ আমলাতন্ত্রের কাঠামো,ক্রমসোপান,এবং কর্মপদ্ধতির ওপর জোর দেন,যা আধুনিক জনসেবাকে আরও সুসংগঠিত ও দক্ষ করে তোলে।
যুগে যুগে আমলাতন্ত্র
প্রাচীনকালে জনসেবা বলতে মূলত রাজতন্ত্রের অধীনে রাজকীয় কর্মকর্তাদের শাসনকার্য পরিচালনা ও হুকুম পালন করাকে বোঝানো হতো। সেই সময়ে জনগণের অধিকারের ধারণাটি প্রায় অনুপস্থিত ছিল, এবং রাজকর্মচারীরা প্রায়শই জনগণের কাছে ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে proconsul বা privatus-এর মতো পদাধিকারীরা ছিলেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাদের মূল কাজ ছিল সম্রাটের আদেশ কার্যকর করা, কর সংগ্রহ করা এবং আইন প্রয়োগ করা। জনগণের কাছে তারা ছিলেন সম্রাটের প্রতিভূ এবং তাদের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। অনেক সময় এই কর্মকর্তারা নিজেদের ক্ষমতা অপব্যবহার করতেন, যা জনগণের মধ্যে তাদের প্রতি ভয় তৈরি করত। রোমান নাগরিকদের জন্য আইন থাকলেও, অধিকৃত প্রদেশগুলোর জনগণের ওপর তাদের হুকুম ছিল চূড়ান্ত।
প্রাচীন চীনে ম্যান্ডারিন নামে পরিচিত আমলারা সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী শ্রেণি ছিলেন। তারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন এবং রাষ্ট্রের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে আসীন হতেন। তাদের হাতে ছিল জনগণের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ। তাদের কাজ ছিল আইন প্রয়োগ, কর সংগ্রহ এবং বিচারকার্য পরিচালনা। যদিও তাদের মেধা ও যোগ্যতা ছিল, তাদের প্রশাসনিক কঠোরতা এবং প্রায়শই জনগণের প্রতি অসংবেদনশীল মনোভাবের কারণে তারা জনমনে এক ধরনের ত্রাসের সৃষ্টি করতেন। সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস পেত না, কারণ তারা জানত যে এর ফল ভালো হবে না।
মুঘল আমলে আমিল বা সুবাদার নামক কর্মকর্তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন। আমিলরা ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় তারা অনেক সময় জনগণের উপর অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করতেন এবং নির্যাতনের আশ্রয় নিতেন। সুবাদাররা ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর এবং তাদের হাতে ছিল বিশাল ক্ষমতা, যা জনগণের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করত। সাধারণ মানুষ তাদের দেখলেই শ্রদ্ধা ও ভয়ের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে মাথা নত করত, কারণ তারা জানত যে এই কর্মকর্তাদের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করা অসম্ভব।
ব্রিটিশ যুগে আমলাদের পদবী ছিল সিভিল সার্ভেন্ট । তাদের প্রধান পদ্গুলো ছিল জেলা কালেক্টর, বিভাগীয় কমিশনার এবং সচিব। ব্রিটিশ আমলারা জনগণের প্রয়োজন ও কল্যাণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ পালন করতেন এবং তাদের শাসনকে শক্তিশালী করতে কাজ করতেন। তাই তারা ব্রিটিশ-বান্ধব হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন।
গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনসেবার অভিমুখ বদলঃ জনগণ-শোষণ থেকে নাগরিক-তোষণ
গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো ‘জনগণই ক্ষমতার উৎস’ এই দর্শন। গণতন্ত্রে ভোটাধিকারের মাধ্যমে মানুষ তার পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, যার ফলে তারা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। মানব ইতিহাসে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা আগে রাজতন্ত্র বা স্বৈরাচারী শাসনের মতো ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল। এ বিষয়ে ভারতীয় বাঙ্গালী নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তার ‘দ্যা আইডিয়া অব জাস্টিস’ বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, গণতন্ত্র কেবল একটি শাসনব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি প্রক্রিয়া যেখানে জনগণের মতামত ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গণতন্ত্রের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। জনকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানো—এসবই গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব। তবে, সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই যে মানব কল্যাণ পুরোপুরি নিশ্চিত হয়, তা বলা যায় না। কারণ, অনেক সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জনকল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল তার ‘অন লিবার্টি’ গ্রন্থে বলেছেন, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যেকোনো ভালো রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর গণতন্ত্র এই লক্ষ্য অর্জনের একটি কার্যকর মাধ্যম হতে পারে। সার্বিকভাবে এটাই সত্য যে, গণতন্ত্র মানুষকে যে স্বীকৃতি এবং মানবকল্যাণকে যে গুরুত্ব দিয়েছে, তা মানব ইতিহাসের এক বড় অগ্রগতি এবং এই দর্শন থেকেই জনসেবার অভিমুখ জনগণ শোষণ ও রাজাদের তোষণ থেকে জনগণের কল্যাণ ও জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রুপান্তরিত হয়েছে।
বাংলাদেশে নাগরিকমুখি জনসেবার প্রসার ও বিকাশ
বর্তমানে বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বে যে জনসেবামুখি প্রশাসন বিদ্যমান রয়েছে তা কিন্তু এদেশের ব্রিটিশ কিংবা পূর্বযূগের জনবিদ্বেষী আমলাতন্ত্রের পরিবর্তিত রুপ। গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত নাগরিক-মুখি সংবিধানে তাই নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন এবং মেধা ও ন্যায্যতার ভিত্তিত্তে সিভিল সার্ভিস নিয়োগের মূলনীতি সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিদ্যমান সরকারি চাকুরিজীবিদের সচেতন থাকা আবশ্যক যে, শোষণমূলক নাগরিক-বিদ্বেষী জনসেবার খোলস এর বদলে বিদ্যমান এই নাগরিক-বান্ধব জনসেবা কাঠামো পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছে হাজার হাজার বছর। জীবন দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, নতুন দর্শন হাজির করতে হয়েছে শত শত দার্শনিকদের যার সর্বশেষ আন্দোলন হচ্ছে ‘ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা ইনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট’। মানবসভ্যতার যে বিবর্তন-ধাপে আমরা বর্তমানে অবস্থান করছি তার অতীত ইতিহাস সঠিকভাবে জানা থাকলেই কেবল সম্ভব নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা। আমলাতন্ত্র বা সরকারি চাকুরীজীবী প্রতিটি ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সচেতন করা না গেলে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের পরিবর্তে একেকজন তাদের পূর্বসূরীদের মত দানব হয়ে উঠতে পারে, কারণ তারা তাদের রক্তে বহন করছে অতীতের সেই শোষকরুপি আমলাদের জীন বা ডিএনএ। আর এদেরই নমুনা হিসাবে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে জনসম্মুখে আবির্ভূত হয় ছাগলকান্ডের সেই কুখ্যাত এনবিআর কর্মকর্তা মতিউর রহমান কিংবা পিএসসির কর্মচারী আবেদ আলীরা।
নাগরিক-বান্ধব জনসেবার বৈশ্বিক এই ধারণার বিকাশের ইতিহাস জানা ও অনুধাবন করা প্রয়োজন সরকারী দপ্তরে কর্মরত সকলের। এ বিষয়টি আরো গভীরভাবে উপলব্ধিতে থাকা প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা দেশ পরিচালনায় নেতৃত্বদানকারী রাজনীতিবিদদের। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অধিকার আদায়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলগুলোর। একই সাথে এ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট নাগরিকদেরও তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত যাতে আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের অধিকারের বন্দোবস্ত করতে পারেন। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, নেপালের গণ-আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ৩৬-জুলাই-বিপ্লব (বর্ষা-বিপ্লব) মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত চুক্তিভিত্তিক জনসেবা নিশ্চিত করারই এক আন্দোলন মাত্র।
লেখক: উপপরিচালক, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, mahbub.cn@gmail.com