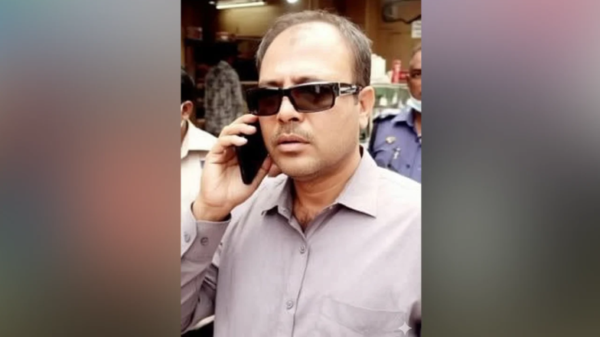‘এক কিডনির গ্রাম’– বাংলাদেশ থেকে ভারতে অঙ্গ পাচারের ভয়াবহ চিত্র

- আপডেট সময় বুধবার, ১৬ জুলাই, ২০২৫
- ১৩৩ বার দেখা হয়েছে

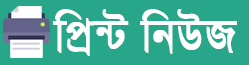
বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার বাইগুনি নামক ছোট্ট গ্রামটি এখন পরিচিত ‘এক কিডনির গ্রাম’ নামে। দারিদ্র্যের ফাঁদে পড়ে গ্রামের বহু মানুষ ভারতে গিয়ে কিডনি বিক্রি করছেন পাচারকারীদের মাধ্যমে। আল জাজিরার সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভয়াবহ এই চিত্র—যেখানে মানবিক দুর্দশা আর দুর্বল সীমান্ত ব্যবস্থাপনার সুযোগে গড়ে উঠেছে একটি বহুজাতিক কিডনি পাচার নেটওয়ার্ক।
প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়, ৪৫ বছর বয়সী সফিরউদ্দিন ২০২৪ সালে ভারতে গিয়ে ৩.৫ লক্ষ টাকায় নিজের একটি কিডনি বিক্রি করেন। উদ্দেশ্য ছিল সন্তানদের জন্য ঘর তৈরি ও দারিদ্র্য ঘোচানো। কিন্তু এখন তিনি শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিদিনের কাজ করতে হিমশিম খাচ্ছেন।
“আমি কিডনি দিয়েছিলাম ভালো কিছুর আশায়। এখন শুধু কষ্ট আর আফসোস,” — বলেন সফিরউদ্দিন।
পাচারকারীরা তার জন্য মেডিকেল ভিসা, ফ্লাইট, নথিপত্র এমনকি ভুয়া আত্মীয়তার কাগজ তৈরি করে। অস্ত্রোপচারের পর ওষুধ, প্রেসক্রিপশন তো দেওয়া হয়নি বরং তার পাসপোর্টটিও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।
আল জাজিরার তথ্যমতে, বাইগুনিসহ পুরো কালাই উপজেলা কিডনি পাচারের একটি সক্রিয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। BMJ Global Health-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় জানা যায়, এ অঞ্চলের প্রতি ৩৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির একজন কিডনি বিক্রি করেছেন।
৮৩ শতাংশ দাতা কিডনি বিক্রির কারণ হিসেবে দারিদ্র্যকে দায়ী করেছেন। কেউ ঋণ, কেউ মাদকাসক্তি কিংবা জুয়ার কারণে এই পথে হাঁটেন।
প্রতিবেদনে আরও উঠে আসে ৪৫ বছর বয়সী বিধবা জোসনা বেগমের ঘটনা। দুই সন্তানকে নিয়ে জীবন চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এক দালালের প্ররোচনায় দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে ২০১৯ সালে কিডনি বিক্রি করেন ভারতের একটি হাসপাতালে। প্রাথমিকভাবে ৭ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও হাতে পান মাত্র ৩ লাখ টাকা। কিছু টাকা দিয়ে তারা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। স্বামীও তাকে ছেড়ে যায়। এখন আছে কেবল শরীরের ব্যথা আর ওষুধের খরচ।
এক সময়ের ব্যবসায়ী মো. সজল (ছদ্মনাম) ২০২২ সালে কিডনি বিক্রি করেন ভারতের একটি হাসপাতালে। প্রতিশ্রুতি ছিল ১০ লাখ টাকা, পান ৩.৫ লাখ। পরে তিনিও দালাল চক্রে জড়িয়ে পড়েন। দালালদের হয়ে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারতে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য পাঠাতেন। পরে আর্থিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে চক্র ত্যাগ করেন এবং এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
ভারতে ১৯৯৪ সালের মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন অনুযায়ী, কিডনি দান কেবল ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যেই বৈধ। অন্যদের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দালালরা ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র, ডিএনএ টেস্ট এবং নোটারি সনদের মাধ্যমে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক দেখিয়ে এই আইনকে ফাঁকি দেয়।
মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অঙ্গ প্রতিস্থাপন টাস্কফোর্সের সদস্য মনির মনিরুজ্জামান আল জাজিরাকে বলেন,
“কাগজপত্র ঠিক থাকলেই হাসপাতাল অনুমোদন দিয়ে দেয়। তারা আর বেশি কিছু খোঁজে না, কারণ প্রতিটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট মানে বড় অঙ্কের মুনাফা।”
আল জাজিরা জানায়, একেকটি কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের জন্য গ্রহীতারা প্রায় ২২ থেকে ২৬ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করেন। কিন্তু দাতারা পান ৩–৫ লাখ টাকা। বাকি অর্থ ভাগ হয়ে যায় পাচারকারী, চিকিৎসক, জাল নথি প্রস্তুতকারীদের মধ্যে।
বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে, তারা পাচার চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারতে দিল্লি পুলিশ একাধিক অভিযানে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের গ্রেফতার করেছে। ২০২৪ সালে এক চিকিৎসককে ১৫টি বাংলাদেশি রোগীর অবৈধ কিডনি প্রতিস্থাপনের দায়ে আটক করা হয়।
তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, sporadic ধরপাকড়ে এই ব্যবসার ভিত্তি নড়ে না। বরং পাচারকারীরা স্থান পরিবর্তন করে আবারও শুরু করে।
ভারতের Kidney Warriors Foundation-এর সিইও বসুন্ধরা রাঘবন মনে করেন, এই অবৈধ চক্র পুরোপুরি বন্ধ না হলেও দাতাদের জন্য একটি ন্যূনতম সুরক্ষা নীতিমালা থাকা উচিত।
“দাতাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পরবর্তী চিকিৎসা সেবা, ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে এই ব্যবসার ভয়াবহতা কিছুটা হলেও কমানো সম্ভব,” — বলেন তিনি।
কালাইয়ের বাইগুনিতে এখন সফিরউদ্দিন দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাটান বাড়িতে। শরীরে যন্ত্রণা, কাজে অক্ষমতা আর মনে গভীর হতাশা।
“বাচ্চাদের জন্য ভেবেছিলাম ঘর করব। এখন ওরা পাচ্ছে এক অসুস্থ বাবা আর ভাঙা স্বপ্ন। ওরা (দালালরা) আমার কিডনি নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।”